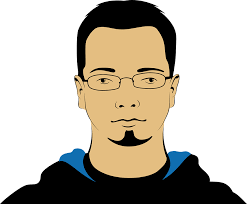

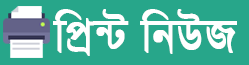
মেঘালয় থেকে বাংলাদেশে এই সাদা পাথর আসার পুরো প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক ধাপে সম্পন্ন হয়।
বিশেষ প্রতিবেদন,আদালত বার্তাঃ ১৭ আগস্ট ২০২৫।
ভারতের মেঘালয় মালভূমি (Meghalaya Plateau) মূলত গ্রানাইট ও নাইস-এর মতো শক্ত শিলা দ্বারা গঠিত।
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বৃষ্টি, বাতাস এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে এই শক্ত শিলাগুলো ক্ষয় হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে শিলা থেকে কোয়ার্টজের মতো কঠিন খনিজগুলো আলাদা হয়ে নুড়িতে পরিণত হয়।
বর্ষাকালে বা পাহাড়ি ঢলের সময়, খরস্রোতা পাহাড়ি নদীগুলো (যেমন পিয়াইন ও ধলাই) শক্তি নিয়ে নেমে আসে। এই প্রবল স্রোত তখন ক্ষয়প্রাপ্ত নুড়ি, বালি ও পাথরগুলোকে ঠেলে বাংলাদেশের দিকে নিয়ে আসে।
নদীগুলো যখন মেঘালয়ের খাড়া ঢাল বেয়ে বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন এদের গতি হঠাৎ করে কমে যায়।
ফলে, নদীগুলো আর ভারী পাথর ও নুড়িগুলোকে বহন করতে পারে না। তখন এই পাথরগুলো নদীর বাঁকে বা চরে জমা হতে থাকে। ভোলাগঞ্জ ও জাফলং ঠিক এমনই দুটি স্থান।
এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে ভূতত্ত্বের ভাষায় প্লাসার ডিপোজিট (Placer Deposit) বলা হয়।
এখন যেহেতু আমরা জানি এই পাথরগুলো একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সীমান্তে এসে জমা হয়, সেহেতু আমাদের পরবর্তী বিষয়গুলো হলো সম্পদের পরিমাণ (Estimated Resources) এবং খনির প্রকৃতি (Nature of Deposit)।
এই পাথরগুলো কোনো সুরঙ্গ বা গভীর গর্ত খুঁড়ে তৈরি করা খনি থেকে তোলা হয় না।
এগুলো সরাসরি নদীর তলদেশ এবং নদীর তীরে জেগে ওঠা চর থেকে সংগ্রহ করা হয়। তাই এর খনির প্রকৃতি হলো উন্মুক্ত বা সারফেস ডিপোজিট (Open/Surface Deposit)।
ভূতাত্ত্বিক ভাষায়, একে প্লাসার ডিপোজিট (Placer Deposit) বা এলুভিয়াল ডিপোজিট (Alluvial Deposit) বলে, যেখানে মূল্যবান খনিজ (এখানে পাথর) নদীর স্রোতের মাধ্যমে এক জায়গায় জমা হয়।
এর সাথেই আমাদের পরের দুটো বিষয় সম্পর্কিত।
সম্পদ পরিমাণ (Estimated Resources) ও খনির প্রকৃতি (Nature of Deposit)
খনির প্রকৃতি: এটি একটি নবায়নযোগ্য (renewable) ভান্ডার। প্রতি বছর বর্ষায় উজান থেকে নতুন পাথর ভেসে এসে জমা হয়, তাই এর পরিমাণ পুরোপুরি নির্দিষ্ট নয়। পুরনো পাথর তুলে ফেলার পরেও নতুন করে পাথর এসে জমা হয়।
সম্পদ পরিমাণ: যেহেতু এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই এর মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (GSB) বিভিন্ন সময়ে জরিপ চালিয়েছে। যেমন, শুধু ভোলাগঞ্জেই প্রায় ১০.৬ কোটি ঘনফুট পাথরের মজুদ অনুমান করা হয়েছিল। তবে এই সংখ্যাটি প্রতি বছর বদলায়।
সবচেয়ে বড় মজুদ: সবচেয়ে বড় এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মজুদটি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জে অবস্থিত।
ক্ষুদ্র মজুদ: জাফলং, বিছানাকান্দি এবং লোভাছড়ার মতো অন্যান্য স্থানেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মজুদ রয়েছে, তবে ভোলাগঞ্জের তুলনায় কম।
উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদরা প্রথম এই স্তরকে বর্ণনা ও মানচিত্রে চিহ্নিত করেন সিলেট অঞ্চলের (তৎকালীন আসাম প্রদেশ) কাছাকাছি এলাকায়, তাই নাম হয় Sylhet Limestone।
আসলে এই স্তর শিলং মালভূমি থেকে শুরু করে মেঘালয়, আসাম ও সিলেট সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত।
খনি মেঘালয়ে হলেও বাংলাদেশ কিভাবে সুবিধা পায়?
মেঘালয়ের পাহাড় থেকে এই পাথর নদীপথে (ধলাই, পিয়াইন, গোয়াইন) নেমে এসে সিলেটের পাদদেশে জমা হয় – প্রাকৃতিক সঞ্চয়ন এলাকা (ভোলাগঞ্জ, জাফলং, বিছানাকান্দি ইত্যাদি)।
বাংলাদেশে নদী তীরের এই সঞ্চিত পাথর তুলতে খনি খনন লাগে না, শুধু সংগ্রহ করলেই হয়।
খনি মেঘালয়ে তাহলে তো বেশির ভাগ সম্পদই মেঘালয়েই থেকে যাওয়ার কথা। তাই না?
হ্যাঁ, ভূতাত্ত্বিকভাবে ঠিক তাই – মূল স্তর ও খনির বড় অংশ মেঘালয়ের ভেতরে।
কিন্তু পাথরটা যেহেতু পাহাড়ি নদীর মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে আসে, তাই মেঘালয়ের ভেতরে থেকে গেলেও এর একটা বড় অংশ প্রাকৃতিকভাবে সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে জমা হয়।
এইভাবে ধরতে যায় –
মেঘালয়ে মূল উৎসঃ
চুনাপাথরের স্তর পাহাড়ের ভেতরে থাকে, সেখানে সরাসরি খনন করে পাথর তোলা হয় (ভারতীয় কোম্পানি যেমন Lafarge, Komorrah ইত্যাদি)।
= এগুলো ভারতের বাজারে যায় বা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়।
বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সঞ্চয়নঃ
ভারী বর্ষা + পাহাড়ি নদীর তীব্র স্রোত = পাথর, নুড়ি, বালি পাহাড় থেকে ভেসে এসে সিলেটের ভোলাগঞ্জ, জাফলং, বিছানাকান্দি ইত্যাদিতে জমা হয়। এই অংশ বাংলাদেশে তুলতে আলাদা খনি খনন লাগে না। বাংলাদেশ বিনা খরচে প্রাকৃতিক “ডেলিভারি” পায়।
এই সাদা পাথরগুলো অত্যন্ত শক্ত ও টেকসই হওয়ায় বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পের মূল কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভবন, সেতু, কালভার্ট, এবং সড়ক নির্মাণে যে কংক্রিট তৈরি করা হয়, তার জন্য এই পাথর অপরিহার্য। সিলেট থেকে এই পাথর সারা দেশে সরবরাহ করা হয়।
ভোলাগঞ্জ ও জাফলং অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের জীবিকা এই পাথর উত্তোলনের ওপর নির্ভরশীল। পাথর সংগ্রহ, ভাঙা, এবং পরিবহনের সাথে বিশাল এক কর্মী বাহিনী জড়িত।
কিন্তু,
অপরিকল্পিতভাবে এবং অতিরিক্ত পাথর উত্তোলনের ফলে নদীর তীর ভাঙন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের (aquatic ecosystem) মারাত্মক ক্ষতি হয়। বোমা মেশিনে সাহায্যে নদী থেকে পাথর তোলার কারণে পরিবেশের ওপর চাপ বেড়েছে এবং এই দোহাই দিয়ে শুরু হয় এক নতুন খেলা!
পরিবেশবাদীরা মাঠে নেমে পড়েন! ঠুকে দিলেন রিট!
২০১৮ সালে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর দায়ের করা রিটের প্রেক্ষিতে সিলেটের পাথর কোয়ারিগুলোকে সরকারিভাবে Environmentally Critical Area (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।
এর ফলে জাফলং, সাদাপাথরসহ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো থেকে পাথর উত্তোলন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যা সরকারি আদেশের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ায় স্থানীয় কোয়ারির শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখোমুখি হন।
২০১৮ সাল থেকে এই নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘকাল ধরে বহাল থাকে এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বজায় থাকে, যদিও দেশের অন্যান্য এলাকায় ধীরে ধীরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা শুরু হয়।
২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সকল পাথর কোয়ারিতে উত্তোলন স্থগিতের নির্দেশ দেয়, যা সিলেটের কোয়ারিতেও প্রযোজ্য থাকে। এই নির্দেশের ফলে পাথর উত্তোলন “পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত” বন্ধ থাকে।
শেষ পর্যন্ত ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ সালে পূর্বের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়, ফলে সিলেটসহ দেশের সব পাথর ও বালু মহাল থেকে পাথর, বালি ও সাদা মাটি উত্তোলনের উপর আর কোনো বিধিনিষেধ থাকে না।
তবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলো এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করে।
সামগ্রিকভাবে, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সিলেটের পাথর কোয়ারিতে দীর্ঘকালীন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছিল, যা স্থানীয় পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।
====
ধরে নেন, এসবই উপরওয়ালার রহমত হিসেবে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, সেই রহমত গ্রহণ না করলে কি হতে পারে?
সবার জানা সিলেটের ভয়াবহ বন্যার কথা?
দীর্ঘ ১১ বছর যে অঞ্চলে বন্যা হয়নি হঠাৎ সে অঞ্চলে বন্যা হয় ২০১৮ তে। তারপর ২০১৯ ও ২০২০, পর পর ৩ বছর সিলেটে বন্যা হয়! আর ২০২২ ও ২০২৪ এ যে বন্যা হয়েছে তা ছিলো ১২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভয়াবহ বন্যা!
এই বন্যার অনেক গুলো কারণ থাকতেই পারে। কিন্তু আমার দৃষ্টি পড়ে অন্য একটি ঘটনায়।
২০১৮ সালে বছরের শুরু থেকেই সিলেটে পাথর উত্তোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়, আর একই বর্ষা মৌসুমেই বড় বন্যা দেখা দেয়।
নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর মাত্র ৪–৬ মাসের মধ্যেই এই বন্যা হওয়ায় প্রভাব থাকলেও তা দ্রুত বোঝা কঠিন ছিল।
পরের বছর ২০১৯ সালে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে এবং প্রায় ১২–১৫ মাস পর আবারও বড় বন্যা ঘটে। দীর্ঘ ব্যবধানের কারণে এখানে নদীর পলি জমা, পানির প্রবাহের ধরণ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় প্রভাব ফেলতে পারে।
২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সারা দেশে পাথর উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ জারি হয়, আর প্রায় চার মাস পর জুন–জুলাই মাসে বন্যা হয়। এই স্বল্প ব্যবধানে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব আলাদা করে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়।
অন্যদিকে, ২০২২ সালের রেকর্ড বন্যার সময় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছিল প্রায় চার বছর ধরে।
এত দীর্ঘ সময় পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকার পরও ভয়াবহ বন্যা হওয়া প্রমাণ করে যে শুধুমাত্র উত্তোলন বন্ধ রাখা বন্যা প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়; বরং অতিবৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পানি এবং নদীর ধারণক্ষমতা হ্রাসের মতো প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
একইভাবে, ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় নিষেধাজ্ঞা চলছিল প্রায় ছয় বছর ধরে, তবুও বন্যার তীব্রতা কমেনি।
সুতরাং দেখা যায়, স্বল্প ব্যবধানের ক্ষেত্রে (যেমন ২০১৮ ও ২০২০) নিষেধাজ্ঞা ও বন্যা প্রায় একই বর্ষায় মিলে গেছে, আর দীর্ঘ ব্যবধানের ক্ষেত্রেও (যেমন ২০২২ ও ২০২৪) পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকলেও বন্যার প্রকোপ কমেনি।
ফলে অনুমান করা যায়, পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখা স্থানীয় নদীর কিছু পরিবেশগত ক্ষতি কমাতে পারে, কিন্তু বড় মাপের বন্যা প্রতিরোধে এর ভূমিকা সীমিত, কারণ মূল কারণগুলো প্রাকৃতিক ও বৃহত্তর ভৌগোলিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।
যেই সময়টিতে আমাদের দেশে পাথর উত্তোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা চলে, সে সময়ে সীমান্তের ওপাশে শত শত পাথর উত্তোলন করার কোয়ারি স্থাপন করে, পাহাড় কেটে বিপুল পরিমাণ পাথর সংগ্রহ করে।
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থানগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বিছানাকান্দিতে পাথরের পরিমাণ অনেক বেশি ।
।